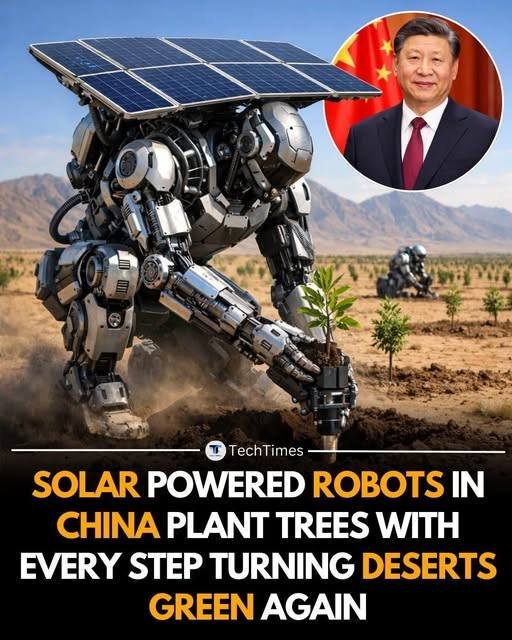শশঙ্ক-র সময় থেকে সেন রাজা পর্যন্ত (৫৯৩-১১৯৩) ৬০০ বছর এরাই বাংলার স্বাধীন শাসক ছিল। কায়স্থ-রা মূলত রাজা সামন্ত জমিদার হত। ব্রাক্ষণরা হত শিক্ষক অধ্যাপক মন্ত্রী, বৈদ্যরা হত চিকিৎসক, বেনেরা হত ব্যবসায়ী। এরাই ছিল বর্তমান বিহারের দ্বারভাঙ্গা থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এলিট সমাজ। ১১৯৩ সালে বখতিয়ার খিলজি-র আগমণে তারা প্রথমে পশ্চীম অংশে ও তার ৫০ বছর পরে পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতা হারায়। তবে বখতিয়ার মারা যাওয়ার পর থেকেই কাবাব-রা বুঝে যায় নব্য আগত তুর্কি আফঘান-দের সাথে জোট বাঁধার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তুর্কি আফঘানরা নগর জীবন পছন্দ করছে, নতুন নগর বানাচ্ছে, নতুন ব্যবসা ও প্রযুক্তি আনছে। তারা গ্রামে থাকতে পছন্দ করছেনা এবং গ্রাম থেকে খাজনা আদায় করার জন্যে কাবাব-দেরই স্মরণাপন্ন হচ্ছে। আইওয়াজ খিলজি যখন ১২১০ সালে দিল্লী সুলতান-কে অস্বীকার করে স্বাধীন লখনোউতি সালতানাত ঘোষণা করেন, কাবাব-রা বুঝে যায় তুর্কি-দের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাদের পক্ষেই যাবে।
আইওয়াজ বেশি দিন দিল্লীর সামনে টিকতে না পারলেও কাবাব-রা তুর্কি-দের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের গন্ধ পেয়ে যায়। আস্তে আস্তে নব্য আগত তুর্কি আফঘান-দের সাথে জোট বাঁধা শুরু করে কাবাব-রা। দিল্লীতে জালালুদ্দীন খিলজি ও আলাউদ্দীন খিলজি ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে নীম্ন তুর্কিদের উত্থান হয় উচ্চ তুর্কিদের পতন হয়। আআলুদ্দীন খিলজি-কে বেদের দেবতা ইন্দ্র পুরন্ধর-এর সঙ্গে তুলনা করে ব্রাক্ষণ-রা শ্লোকও লেখে। তুঘলক শাসনকালে প্রদেশগুলোয় স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়। প্রথমে মোবারক শাহ ও পরে ইলিয়াস শাহ-র নেতৃত্বে বাংলা স্বাধীন সুলতানাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মনে রাখা দরকার ইলিয়াস শাহ-র স্ত্রী ছিলেন পুষ্পবতী ভট্টাচার্য (ইসলাম ধর্ম নেওয়ার পরে তার নাম হয় ফুল্লরা বেগম)। এছাড়াও ইলিয়াস শাহ-র হয়ে একডালা যুদ্ধে দিল্লির সাথে যুদ্ধ করেন অজস্র কাবাব সামন্ত ও সেনা যেমন- শিকাই সান্যাল, সুবুধিরাম ভাদুরী, জগানন্দ ভাদুরী ও কেশবরাম ভাদুরী। ইলিয়াস-এর নেতৃত্বেই তৈরি হয় স্বাধীন বাংলা সালতানাত ১৩৫৩-৫৬ সালে। জন্ম হয় বাঙালি মুসলমানের। বাংলা সালতানাতই প্রথম বাংলা ভাষা-কে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়। তবে একথাও মনে রাখা দরকার দেক্কান বাহামণি সুলতানরাও তেলেগু ভাষা-কে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছিল। বাহামণি নামটাই আসে ব্রাক্ষণ থেকে কারণ ব্রাক্ষন সন্তান হাসান গাঙ্গু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরে বাহামণি সালতানাত বানায়। যাই হোক বাংলায় ফেরা যাক। পাল রাজাদের আমলে বাঙালি যখন বিশ্ব বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণকেন্দ্র ছিল সেই সময়েও বাংলা হরফে সংস্কৃত লেখারই চল ছিল। বাংলা হরফে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা মূলত বাংলা সুলতান-দেরই কীর্তি। তবে বাংলা সালতানাত-এর অঙ্গ কাবাব-রা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তাই রাজা গনেশও সালতানাত-এর ক্ষমতা নিয়ে নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন। গণেশের পুত্র শাহজাদা যদুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দীন হওয়া প্রমাণ করে কাবাব-রা ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করেছিল ব্যপক হারে ওই সময়ে। শেষ বাংলা সুলতান দাউদ খান কুররাণির প্রধান সেনাপতি ছিল রাজীব লোচন রায় যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হয়ে উঠেছিল কালাপাহাড়। ১৫৭৫-এর রাজমহলের যুদ্ধে কালাপাহাড় শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিল বাংলা সালতানাতের হয়েই। বাংলা সালতানাতে (১৩৫৩-১৫৭৫) বাঙালি সুলতান ও অভিজাত-দের সঙ্গে কাবাব-দের একটা শক্তির ভারসাম্য ছিল।
১৫৭৫ থেকে ১৬১১-এর মধ্যে গোটা বাংলা দিল্লীর মোঘল বাদশাহর হাতে যায়। বাঙালি স্বাধীনতা হারায়। কাবাব-দের চোখে বাঙালি মুসলমান আর সার্বভৌম থাকলনা। যশোর ১৬১১ সালে পতন হয় এবং তারপর থেকে কাবাব-রা আর সেভাবে কখনো সামরিক শক্তি দেখাতে পারেনি। মোঘল আঘাতে তারা যুদ্ধ থেকে অনেকটাই সরে আসে। বহু বাঙালি মুসলমান এই সময়ে কৃষি কাজ শুরু করে। কাবাব-দের চোখে ক্রমেই বাঙালি মুসলমান সামাজিক স্ট্যাটাস হারায়। কাবাব-রা দিল্লী থেকে আগত অবাঙ্গালি মুসলমান ও রাজস্থানের হিন্দু-দের অধস্তন হয়ে যায়। শক্তির ভারসাম্যে কাবাব-রা খুবই দুর্বল ছিল। বাংলার ব্যবসাও চলে যাচ্ছিল মাড়োয়ারী তথা রাজস্থানীদের হাতে। শাসক অবাঙ্গালি মুসলমান-দের প্রতি ঘৃণা আর কৃষক বাঙালি মুসলমান-দের প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মাতে থাকে কাবাব-দের মধ্যে। ১৭০৭ সালে ওউরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে দ্রুতই মোঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। মাড়োয়াড়ি উমি চাঁদ ও জগত শেঠদের সাথে ও উদীয়মান ইংরেজদের সাথে জোট বেঁধে ১৭৫৭ সালে ৫৫০ বছরের মুসলমান শাসন খতম করে বাঙালি কাবাব-দের একটা অংশ। মাড়োয়াড়ি-দের ক্ষমতা বাংলার ব্যবসায়ে বেড়ে যাওয়ার কথ ইংরেজরা আসার পরে। কিন্তু কাবাব-রা দারুণভাবে ইংরেজ-দের সাথে জোট বেঁধে বাঙলার ব্যবসা হাতে নিতে সক্ষম হয়। সেই ব্যবসার টাকায় চীরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর জমিদারী কিনে বসে তারা। ১৮৫০ পর্যন্ত কাবাব-রা ব্যবসা-তে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখায়। মেকলে-র মতে কাবাব-দের মতো ধৈর্যশীল বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী দঃ এশিয়াতে আর নেই। এসময় তারা বাংলার হস্তশিল্প শেষ করে, বাংলার কৃষি সমাজকে দারুনভাবে শোষণ করে। কেবল কোলকাতা বন্দরের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করেই তাদের ব্যবসা চলছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর এরকম সময়েই পৃথিবীর অন্যতম ধনী ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু ১৮৫০-এর পরে যত পশ্চীম বিশ্ব অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে শুরু করে ততই ভারতের পশ্চীমের বন্দরগুলোর গুরুত্ব বেড়ে যায় কোলকাতার তুলনায়। ব্যবসা হারাতে থাকে কাবাব-রা। সরকারী উচ্চপদস্থ চাকরীমুখী হয়ে যায় কাবাবরা। জ্ঞানে পারদর্শিতা দেখালেও ব্যবসায়ে বাংলাতে ক্রমেই মাড়োয়াড়িদের কাছে কোণঠাসা হয়ে যায় কাবাব-রা। ১৮৯০ থেকে কাবাব-রা মোটামুটি মূল ব্যবসা থেকে উৎখাত হয়ে যায় খোদ বাংলাতেই। মাড়োয়াড়ি-দের হাতেই ইংরেজরা বাংলার ব্যবসা তুলে দেয় ওই সময় থেকেই।
১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ করতে চাইলে কাবাব-রা বাঁধা দেয় শেষ সম্বল পূর্ব বঙ্গের জমিদারী টিকিয়ে রাখতে। সরকারী চাকরী টিকিয়ে রাখতে মুসলমান কৃষক-দের পড়াশুনোরও বিরোধিতা করে কাবাব-রা। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আটকানো গেলেও বিহার উরিশ্যা আসাম হারায় কাবাব-রা। রবীন্দ্রনাথের নোবেল জয় হোক বা সত্যেন বোসের পদার্থবিদ্যা জয় বা জগদীশ চন্দ্র বসুর জীব বিজ্ঞানে জয়- এই সব ব্যক্তি কীর্তির আড়ালে দুর্বলই হচ্ছিল কাবাবরা। বাঙালি মুসলমান-দের পুনরুত্থানও ঠেকানো যায়নি বেশি দিন। একদিকে কাবাব-রা বিচ্ছিন্ন ভাবে ইংরেজ বিরোধিতা করতে থাকে আর অন্যদিকে ভারতীয় রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হতে থাকে। চিত্ত রঞ্জন দাশ ও পরে সুভাষ বসু চেষ্টা করেছিলেন বাংলার রিয়েলিটি মেনে নিয়ে বাঙালি ও অবাঙ্গালি মুসলমান-দের সাথে জোট বাঁধতে কিন্তু কাবাব-দের মূল সমস্যা ছিল অ-কাবাব নীম্ন বর্ণের হিন্দুদের গুরুত্ব বাড়তে থাকা। মাহিষ্য জাতির বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সুভাষ বসুর বিরোধিতা করেন। কাবাব-দের অধিকাংশ তখন মুসলমান বিরোধিতা ও হিন্দু ঐক্যের নামে অ-কাবাব নীম্ন বর্ণের বাঙালি হিন্দুদের সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। বলা বাহুল্য পশ্চীম বঙ্গে যেখানে হিন্দু ঐক্য রাজনীতি দারুণ কাজ করছিল, পূর্ব বঙ্গে জমিদার বিরোধী শ্রেণি সংগ্রাম বেশি শক্তিশালী হয়ে যায়। অধিকাংশ জমিদার কাবাব ছিল পূর্ব বঙ্গে। আর তাই নীম্ন বর্ণের হিন্দু ও মুসলমান জোট করে কাবাব-দের বিরুদ্ধে পূর্ব বঙ্গে। শেষ মেশ কাবাব-রা ১৯৪৬ থেকে ক্রমেই বাংলা ভাগের পক্ষে চলে যায়।
কাবাব-রা পূর্ব বঙ্গ থেকে অধিকাংশই পঃ বঙ্গে চলে আসে ১৯৪৭-৫০-এর মধ্যেই। ফলে তাদের ভারত রাষ্ট্রের নাগরীকত্ব নিয়ে কোনও সমস্যা থাকলনা। আবার দুই বঙ্গেই যেহেতু তাদের জনসংখ্যা শেয়ার ৭% ছিল তাই ১৯৫০-এর পরে পঃ বঙ্গে তাদের শেয়ার ১৩.৪% হয়ে যায়। এভাবেই পঃ বঙ্গে কাবাব-দের শাসন আবারও কায়েম হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে কাবাবদের প্রভাব প্রচণ্ড বাড়ে কিন্তু দিল্লীর অধস্তন হওয়ায় ব্যবসা মাড়োয়াড়িদের হাতেই থেকে যায়। দুনিয়া জুড়ে কমিউনিস্ট ভূমি সন্সকারের আন্দোলন পঃ বঙ্গে নিয়ে আনে কাবাব-রাই। তাদের নেতৃত্বে পঃ বঙ্গের মধ্য বর্ণের জোতদার শ্রেণি রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে যায়। তাই ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই মধ্য বর্ণ জোতদার-দের উত্থান হোলেও পঃ বঙ্গে উচ্চ বর্ণ-রা রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। তবে কাবাব-দের নেতৃত্বে থাকা বামফ্রন্ট সরকার পূর্ণ ভূমি সন্সকার করেনি। আধা ভূমি সন্সকার বা "অপারেশন বর্গা" করেছে। তাই কেবল জমিজাত উৎপাদনের ৫০% থেকে ৭৫% বর্গাদারকে দেওয়া হয়েছে মাত্র, জমির মালিকানা দেওয়া হয়নি।
তৃণমূলের শাসনও প্রচণ্ডভাবে কাবাব প্রভাবাধীন। এই আমলে কাবাব-রা বিশ্ব জুড়ে ইসলাম-এর যে উত্থান তাকে কাজে লাগিয়েছে। পঃ বঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা শেয়ার বাড়তে বাড়তে ৩০% থেকে ৩৫% হয়ে গেছে আজ। মুসলমান ভোট ব্যাঙ্কের ওপর দাঁড়িয়েই তৃণমূল মারফত কাবাব শাসন চলছে এখন পঃ বঙ্গে। কিন্তু দিল্লী ক্রমেই পঃ বঙ্গ, আসাম ও উঃ পূঃ বিহার জুড়ে মুসলমান জনসংখ্যা নিয়ে চন্তিত হয়ে পড়েছে। চীন বাংলাদেশ ও নেপাল মিলে এই অঞ্চলে অনেক কিছুই করে ফেলতে পারে। তাই কাবাব-দের ওপর এখন দিল্লী চাপ দেবে মুসলমানদের সাথে জোট ত্যাগ করতে। কিন্তু কাবাব-রা জানে পঃ বঙ্গ থেকে মুসলমান বিতারিত হলে তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলবে। ব্যবসা পুরোপুরি মাড়োয়াড়ি-দের হাতে, পঃ বঙ্গের নীম্ন বর্ণের হিন্দুরাও তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে কাবাব-দের উচ্ছ্বেদ করতে চায়। তাই পঃ বঙ্গে কাবাব-রাজের ভাগ্য এখন অনেকটাই বাঙালি মুসলমানের সাথে জোড়া। এছাড়াও বাঙালি মুসলমান-দের পেছনে চীন থাকবে। তাই খুব বুঝেশুনে এগোনো দরকার। সময়টা খুব খুব ক্রিটিকাল।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
mythical General 08-April-2025 by east is risingট্রাম্প জিতে আসার পর থেকে চারটে বিষয় পরিস্কারভাবে চাইছেঃ
১) মার্কিন ডলার-এর জায়গায় অন্য কোনো মুদ্রা আন্তর্জাতিক লেনদেনে ব্যবহার করলে সেই দেশ-কে অর্থনৈতিকভাবে শাস্তি দেওয়া হবে,
২) অন্যান্য দেশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত আছে তা কমাতে হবে,
৩) মার্কিন ফেডারেল কর্মী সঙ্কোচন করে সরকারী ব্যয় কমাতে,
৪) গ্রীনল্যাণ্ড বলপূর্বক দখল করবে এবং প্রয়োজনে কানাডাকেও দখল করবে।
প্রথম বিষয় প্রমাণ করে ট্রাম্প মার্কিন হেজিমনি অক্ষত রাখতে চান আর সেই জন্যে অনু কোনও মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক লেনদেনে জায়গা ছাড়তে রাজি নন।
দ্বিতীয় বিষয় বোঝায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সাথে যে বাণিজ্য ঘাটতি বজায় রেখে চলছিল, তা আর করতে চাইছেনা বা করতে পারছেনা। ঘুরিয়ে বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বিশ্ব চাহিদার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল তা আর থাকা সম্ভব হচ্ছেনা। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিষয় কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে একই সাথে হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ মার্কিন ডলার আন্তর্জাতিক লেনদেনে আগের অবস্থানেই থাকবে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে ফেলবে, এটা অর্থনৈতিকভাবেই সম্ভব নয়।
তৃতীয় বিষয় প্রমাণ করে মার্কিন সরকারের খরচ কমানো প্রয়োজন। অর্থাৎ মার্কিন বাজেট ঘাটতি কমানো গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তে।
চতুর্থ বিষয় প্রমাণ করে যে নিকটবর্তী অঞ্চল দখল করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জমি ও তার সাথে জনসংখ্যা ও অর্থনীতির পরিমাণগত বৃদ্ধি চাইছে ট্রাম্প। এই ক্ষেত্রে হয় সামরিক খাতে ব্যয় বাড়িয়ে কাজ হাসিল করতে হবে নয়তো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সামরিক এসেট উত্তর গোলার্ধে নিয়ে আনতে হবে। যদি তৃতীয় বিষয়কে মাথায় রাখি তবে বলা যায় অন্যান্য জায়গার সামরিক এসেট উত্তর গোলার্ধে মোতায়েন করা হতেই পারে বাজেট ঘাটতি না বাড়নোর জন্যে। আবার কর্মী সংকোচন করে যে আয় হল তা সামরিক খাতে খরচ করে বাজেট ঘাটতি এক রাখাও উদ্যেশ্য হতে পারে।
আমরা এবার দেখি কেন মার্কিন ডলার-কে আন্তর্জাতিক লেনদেনে আগের মতো শক্তিশালী রেখে দিলে মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সাথেই একি থাকবে বা বেড়ে যাবে? একটা দেশের মুদ্রা মূলত দুটো বিষয়-এর ঘনীভূত রূপঃ সামরিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা। সামরিক ক্ষমতার জোড়ে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে কর তোলার ক্ষমতা ছাড়া রাষ্ট্র তৈরি হতে পারেনা। আর রাষ্ট্র সেই সামরিক ক্ষমতার জোড়েই কেবল মুদ্রা প্রদান করতে পারে। রাষ্ট্রের সামরিক ক্ষমতাই কার্যত তার মুদ্রা ব্যবহার নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ ও প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করে। কিন্তু একটা ফিয়াট মুদ্রার মূল্য কি হবে তা নির্ভর করে সেই মুদ্রা যেই রাষ্ট্র প্রদান করেছে তার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন তার ওপর।
অর্থনীতিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারিঃ প্রবাহমান উৎপাদন বা আয় ও সঞ্চিত সম্পদ যেমন কারখানা অফিস খামার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগার স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি। সাধারণত যেখানে উৎপাদন যত বেশি সেখানে সম্পদও তত বেশি। যদি কোনও রাষ্ট্রের অনেক রপ্তানী থাকে আমদানীর তুলনায় তবে তার বৈদেশিক আয় বেশি হবে। তেমনই যদি কোনও রাষ্ট্রের মানুষ বিদেশে গিয়ে অনেক রোজগার করে তার বড়ো অংশ দেশে পাঠায় তাহলেও রাষ্ট্রের বৈদেশিক আয় বাড়বে। তেমনই কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিদেশীরা পুঁজি বা ঋণ লগ্নী করে সম্পদ বাড়ায়। আবার রপ্তানীর চেয়ে আমদানী বেশি হলে বৈদেশিক ব্যয় বাড়ে, দেশে কর্মরত বিদেশিরা বিদেশে আয়ের বড় অংশ পাঠিয়ে দিলেও আয় কমে আবার দেশের লগ্নীকারীরা বিদেশে লগ্নী করলে দেশের সম্পদ কমে। আয় বাড়লে বা কমলে বলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বা বাণিজ্য ঘাটতি। আবার সম্পদে বিনিয়োগ বাড়লে বা কমলে বলে লগ্নি বা পুঁজি খাতে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি।
এবার আমরা এক বাক্যে বলতে পারতাম যে দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ও পুঁজি খাতে উদ্বৃত্ত সবচেয়ে বেশি সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সবচেয়ে ভালো। এবং সেই দেশের মুদ্রাই আন্তর্জাতিক বাজারে চলবে। কিন্তু ব্যপারটা অনেক জটিল। দেখা যায় কোনও দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত সবচেয়ে বেশি আবার অন্য কোনও দেশের পুঁজি খাতে উদ্বৃত্ত সবচেয়ে বেশি। যদি বিশেষ কোনও দেশের উৎপাদন (ও স্বাভাবিকভাবেই সম্পদ) অন্যান্য দেশের থেকে বেশি হয়, তাহলে সেই দেশের মুদ্রাই আন্তর্জাতিক বাজারে চলবে। অতএব সেই মুদ্রার চাহিদা ও মূল্য অনেক বেশি হবে। যদি মুদ্রার মূল্য বেশি হয় তাহলে সেই দেশের উৎপাদিত পণ্য পরিষেবা ও সম্পদের মূল্যও বেশি হবে অন্যান্য দেশের তুলনায়। মজার ব্যপার হল উৎপাদন-এর মূল্য বেড়ে গেলে চাহিদা কমে যায় ও চাহিদা কমে গেলে উৎপাদনও কমে যায়। অথচ সম্পদের মূল্য বেড়ে গেলে চাহিদা বেড়ে যায় এবং সম্পদে আরও বেশি বিনিয়োগ এসে সম্পদের মূল্য ও পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ যেই দেশের মুদ্রা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তার উৎপাদন বিদেশী উৎপাদনের কাছে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হবে আর তার সম্পদের বাজারে আরও বেশি পুঁজি ও ঋণ আসতে থাকবে। অতএব তার বাণিজ্য ঘাটতি বাড়বে আর পুঁজি খাতে উদ্বৃত্ত বাড়বে। অর্থাৎ সেই দেশে উৎপাদন কম হবে কিন্তু সেই দেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে ঋণ নিয়ে অন্যান্য দেশের উৎপাদন কিনে যাবে।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা প্রদানকারী দেশটা যত দিন অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্থনীতিতে অনেক বড় থাকে, ততদিন সমস্যা হয়না। কিন্তু যখন এক বা একাধিক বড়ো অর্থনীতি বাজারে থাকে তখন আন্তর্জাতিক মুদ্রা প্রদানকারী দেশটা কয়েকটা বড় অর্থনীতি সম্পন্ন দেশের দেওয়া ঋণ বা বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শুধু তাইই না, আন্তর্জাতিক মুদ্রা প্রদানকারী দেশ মনে করতে থাকে যে একটা সময় ওই বড় অর্থনীতিগুলো বাড়তে বাড়তে এত বড় হয়ে যাবে যে তার সম্পদের পরিমাণও অনেক বেড়ে যাবে। তখন তারা সমস্ত বিনিয়োগ তুলে নিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা প্রদানকারী দেশ-কে দেউলিয়া করে দিতে পারে।
তাই দেউলিয়া হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা প্রদানকারী দেশ নিজের মুদ্রার অবমুলয়ায়ণ ঘটিয়ে নিজের উৎপাদন-এর মূল্য কমিয়ে চাহিদা বাড়িয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে পারে। ১৯৭১ সালে ব্রেটনুডস চুক্তি ভেঙ্গে পড়ে ডলারের অবমূল্যায়ণ ঘাটনোর ফলে। আবার বাণিজ্য উদ্বৃত্তে থাকা দেশ যদি নিজের মুদ্রার মূল্য আন্তর্জাতিক মুদ্রার তুলনায় বাড়িয়ে দেয়, তাহলেও তার উৎপাদন-এর চাহিদা কমে যাবে এবং বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কমে যাবে। ১৯৮৫ সালে জাপান নিজের মুদ্রার মূল্য বাড়ায় অনেকটা ডলারের তুলনায় যাকে প্লাজা একরড চুক্তি বলে। মনে রাখা দরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালে ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে পশ্চীম জার্মানি ও জাপানের মার্কিন দেশে করা বিনিয়োগের মূল্য কমিয়ে দেয়, আবার ১৯৮৫-তে জাপান-কে মুদ্রার মূল্য বাড়াতে বাধ্য করে। মার্কিনীরা এইভাবে এক তরফা ডলারের অবমূল্যায়ণ করতে পেরেছিল কারন জার্মানি ও জাপানের নিজস্ব সামরিক জোড় ছিলনা। তাই মার্কিন আদেশ মেনে নিতে তারা বাধ্য ছিল।
কিন্তু ২০২৪ সালে এসে দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বজায় রাখা দেশ হল চীন যার নিজস্ব শক্তিশালী সেনাবাহিনী আছে। শুধু তাইই না, জাপান ও জার্মানি-র উৎপাদন যেখানে কখনৈ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাপিয়ে যায়নি, চীনের উৎপাদন সেখানে মার্কিন উৎপাদনকে ছাপিয়ে গেছে। বর্তমানে চীনের শিল্পোৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে ৩ গুণ বড়ো। ক্রয় ক্ষমতার সমতায় (Purchasing Power Parity) মাপলে চীনের মোট উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ২৩% বেশি। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জাপানের জনসংখ্যা যেহেতু মার্কিন দেশের তুলনায় মাত্র এক তৃতীয়াংশ আর জার্মানি এক-পঞ্চমাংশ, তাই জাপান বা জার্মানির পক্ষে কোনও দিনই মার্কিন অর্থনীতিকে ছাপিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্য দিকে, চীনের জনসংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় চার গুন বেশি। তাই চীনের অর্থনীতি- উৎপাদনে এবং সম্পদে- মার্কিন অর্থনীতিকে ছাপিয়ে যাবে সেটাই স্বাভাবিক।
ট্রাম্প জানে যে জাপান বা জার্মানির মতো চীন মার্কিন আদেশ শুনবেনা। চীন এমনিতেই মার্কিন সম্পদের বাজারে বিনিয়োগ কমিয়ে দিয়েছে অনেক। ২০২৪-এ যা ৭৫০ বিলিয়ন ডলার, ২০১১-এ ছিল ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। অথচ বিসাল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত চীনের পক্ষে রয়েই যাচ্ছে। ট্রাম্প তাই ভুল গড় শুল্ক হর বের করেছেন সেই দেশের মার্কিনীদের সাথে থাকা বাণিজ্য উদ্বৃত্তকে সেই দেশের মার্কিন বাজারে করা রপ্তানী দিয়ে। তারপর সেই ভুল গড় শুল্কের অর্ধেক শুল্ক সেই দেশের ওপর চাপিতা দিয়েছে। ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়া বাংলাদেশ ভারত-এর মতো বহু অর্থনীতি আছে যাদের কাছে মার্কিন বাজার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা মার্কিন আমদানীর ওপর শুল্ক কমিয়ে মার্কিন দেশের সাথে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কমাতে সচেষ্ট হবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার মার্কিন ডলারের মূল্য অত্যন্ত বেশি তা আন্তর্জাতিক মুদ্রা বলে। আর তাই শুল্কের হার কমালেও এই সব দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত খুব একটা নাও কমতে পারে। তখন হয়তো ট্রাম্প এই দেশগুলোকে বলবে তাদের প্রয়োজন নেই এমন মার্কিন পণ্য আমদানী করতে কেবল মার্কিনীদের বৈদেশিক আয় বাড়াতে। এরকম সময়ে কিন্তু বলাই ট্রাম্প উৎপাদন বিক্রি করে আয় করছেন না, বরং বল পূর্বক এই সমস্ত দেশের বৈদেশিক আয় কেড়ে নিচ্ছেন। উল্লেখ্য ১৭৫৭ সালে ব্রিটেন কিন্তু বাংলার সাথে "পলাশী যুদ্ধ" করেছিল ব্রিটেনের সাথে চলা বাংলাত বাণিজ্য উদ্বৃত্তকে বল পূর্বক বাণিজ্য ঘাটতি বানাতে। ব্রিটেন পলাশীর যুদ্ধ জেতার পরেই বাংলার হস্ত শিল্প ধ্বংস করে ব্রিটেনের উৎপাদনের বাজার তৈরি করে বাংলায় এবং বাংলার পণ্য ব্যবহারকারী বিশ্বে। চীনের সঙ্গে ১৮৩০-এর দশকে বাণিজ্য ঘাটতি কাটাতে চীনে আফিম বিক্রি শুরু করে ব্রিটেন। আফিম কেনায় বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি হওয়ায় এবং চীনের সমাজে আফিমের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ায় চীনের ছিং সম্রাট আফিম বিক্রি বন্ধ ঘোষণা করলে, ব্রিটেন আফিম বিক্রি করতে না দেয়ার বিরুদ্ধে "আফিম যুদ্ধ" শুরু করে। তাই ট্রাম্প-এর বিশ্ব থেকে বল পূর্বক বৈদেশিক আয় হাতাবার নীতি আসলে খুবই পুরনো পশ্চীমা নীতি।
মূল বিষয় হল ট্রাম্প জানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যত পরিমাণে ঋণ নিচ্ছে বিশ্ব বাজার থেকে তত পরিমাণে আয় করছেনা। ডলার আন্তর্জাতিক মুদ্রা বলে ঋণ করে ব্যয় করে চলেছে মাত্র। এখন ডলারের উচ্চ মূল্যের জন্যে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন করতে পারবেনা মার্কিনীরা। তাই বল পূর্বক ক্রয়ের অযোগ্য উৎপাদন বল পূর্বক চাপিয়ে দিয়ে অন্যান্য দেশের বৈদেশিক আয়েরন অংশ ছিনিয়ে আনলে ঋণ ও আয়-এর অনুপাত সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। বলা বাহুল্য গ্রীনল্যাণ্ড ও কানাডা বল পূর্বক দখল করার পেছনেও একই অভিসন্ধি। অন্যের আয় ও সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে ঋণ ও আয়-এর অনুপাত সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। পশ্চীমের ইউরোপের দেশগুলো যেমন পর্তুগাল স্পেন হল্যাণ্ড ব্রিটেন ফ্রান্স এশীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি দূর করতেই কখণো রাজ্য দখল করে উপনিবেশ করত, কখনো জল দষ্যুগিরি করত, কখনো যুধে বন্দী মানুষকে দাস হিসেবে বিক্রি করত। ট্রাম্প মূলত সেই নীতিতে আবার ফিরছে।
আয় বাড়াবার আরেকটা উপায় হল সরকারী ব্যয় সঙ্কোচন। কিন্তু সামরিক ব্যয় সঙ্কোচন করলে মার্কিন হেজিমনি ও ডলারের রাজত্ব ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই কোপ পড়েছে সরকারী কর্মীদের ওপর। সরকারী কর্মী কমিয়ে আবারও সেই ঋণ আয়ের অনুপাত ঠিক করা। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন মার্কিন সরকারের ঋণ যেভাবে বাড়ছে আয়ের তুলনায় তাতে দেউলিয়া হওয়া সময়ের ব্যপার মাত্র। তাই সাধারণ মধ্যবিত্ত মার্কিনী ও দুর্বল দেশকে লুটে আয় বাড়ানোই ঠিক মনে করছেন ত্রাম্প।
এর অনিবার্য পরিণতি কি? অনেক মানুষ বিশেষ করে ট্রাম্প নিজে প্রায়ই বলে বেড়াছেন যে এর ফলে বিদেশি আমদানী আর মার্কিন ক্রেতা কিনবেনা বরং দেশীয় বিকল্প পণ্য-এর ক্রেতা বাড়বে এবং মার্কিন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বিষয়টা এত সহজ না। শুল্ক চাপালে বিদেশি আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বাড়বে মার্কিন বাজারে। পণ্যের মূল্য বাড়লে, চাহিদা কমে। অর্থাৎ পণ্যের বাজার কমবে। যদি বাজারে মার্কিন বিকল্প আসেও তার মূল্য শুল্ক চাপানোর আগের আমদানীর চেয়ে বেশি হবে। ফলে চাহিদা ও বাজার কমছেই। তবে বেশি সম্ভাবনা অন্য কোনও দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য শুল্ক চাপানো দেশজাত পণ্যের বিকল্প হয়ে উঠবে। অবশ্যই তাহলেও পণ্যের মূল্য বাড়বে এবং বাজার কমবে। এতে কেবল শুল্ক চাপানো দেশের উৎপাদন অন্য দেশে চলে যাবে তাই নয়, মোট চাহিদা কমে যাওয়ায় নতুন উৎপাদনের দেশেও উৎপাদন কমবে আগের দেশে যত উৎপাদন হত সেই তুলনায়। ফলে বিশ্ব উৎপাদন কমবে। ফলে বিশ্বের আয় কমবে এবং এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব থেকে যে আয় করত তা কমবে। ফলে মার্কিন উৎপাদনও কমবে। বিশ্ব উৎপাদন ও মার্কিন উৎপাদন কমবে এবং মার্কিন বাজারে দ্রব্য মূল্য বাড়বে ফলে মুদ্রাস্ফীতি হবে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার বাড়বে। এর ফলে মার্কিন উৎপাদনে বিনিয়োগ কমবে আবার মার্কিন সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যবসা লাভজনক হয়ে উঠবে। বিশ্বের সমস্ত পুঁজি ছুটবে মার্কিন সম্পত্তি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে ফলে মার্কিন ডলার-এর চাহিদা ও মূল্য বেড়ে যাবে। ফলে মার্কিন উৎপাদন-এর মূল্য বিশ্ব ও মার্কিন বাজারে আরও বেড়ে যাবে। ফলে মার্কিন উৎপাদনের চাহিদা কমে যাবে আর তাই মার্কিন উৎপাদনও কমে যাবে। তাই সব শেষে দেখা যাবে মার্কিন শুল্ক আরোপের ফলে উৎপাদন তো বাড়েইনি বরং কমে গেছে।
ট্রাম্প চাইবে মার্কিন বিলাসবহুল পণ্য পরিষেবা দরিদ্র দেশগুলো কিনে মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি কমাক। এইভাবে দরিদ্র দেশগুলোর ধনী শ্রেণি একদিকে বিলাসবহুল পণ্য ব্যবহার বাড়াবে আর অন্যদিকে সেই দেশের বৈদেশিক আয় কমবে যা সেখানে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব তৈরি করে সমাজকেই অস্থিতিশীল করে তুলবে। তাই দরিদ্র দেশগুলোর উচিত মার্কিন বাজারে রপ্তানী করার ওপর নির্ভর না করা। বিকল্প বাজার খোঁজা এবং দেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বাজার বৃদ্ধি কর। আভ্যন্তরীণ বাজার বৃদ্ধির জন্য পরিকাঠামোয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার দিকে নজর দেওয়া দরকার। পৃথিবীতে বড়ো অর্থনীতি ও বাজার হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান। আরব উপকূল, তুর্কিয়ে, রাশিয়া, লাতিন আমেরিকা, ভারত ও দঃ পূঃ এশিয়া মাঝারি মাপের বাজার। চীনে আরও বাজার পেতে চীনা মুদ্রা ইউয়ান ব্যবহার বাড়ানো দরকার। চীন ২০২৫-এর মার্চ মাসেই ডিজিটাল ইউয়ান চালু করেছে যা দিয়ে দঃ পূঃ এশিয়া ও আরব উপকূল মাত্র ৩ সপ্তাহেই ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের লেনদেন করে ফেলেছে। ডলার ব্যাঙ্ক সুইফট মারফত এক একাউন্ট থেক আরেক একাউন্টে যেতে ৩ থেকে ৫ দিন লাগে। সেখানে ডিজিটাল ইউয়ান চলে যাচ্ছে মাত্র ৭ সেকণ্ডে। মার্কিন জিপিএস-এর চেয়ে অনেক বেশি উন্নত চীনা বেইদাউ নেভিগেশন ও কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক সম্মিলিত ডিজিটাল ইউয়ান ব্যবহার বাড়লে, ইউয়ান-এর মূল্য বাড়বে এবং এর ফলে চীনের বাজারে রপ্তানী করা সহজ হবে। তেমনই ইউরো ও জাপানী ইয়েন-এরও ব্যবহার বাড়িয়ে সেখানে বাজার বাড়ানো যেতে পারে। ট্রাম্প যেহেতু মার্কিন বাজার থেকে রপ্তানী মারফত আয় কমিয়েই দিচ্ছে, তাই ডলারের ব্যবহার কমালে স্যাঙ্কশন খেতে হবে, সেই ভয় অমূলক। দুর্বল অর্থনীতিগুলো সাময়িকভাবে মার্কিন আদেশ মেনে রপ্তানী শিল্প বাঁচাক কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে তাদের বিকল্প বাজার খুঁজতে হবে, বিকল্প মুদ্রা ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং দেশের ভেতরে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়িয়ে ও শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে আভ্যন্তরীন বাজার বাড়াতে হবে।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
International geopolitics General USA vs China 08-April-2025 by east is rising